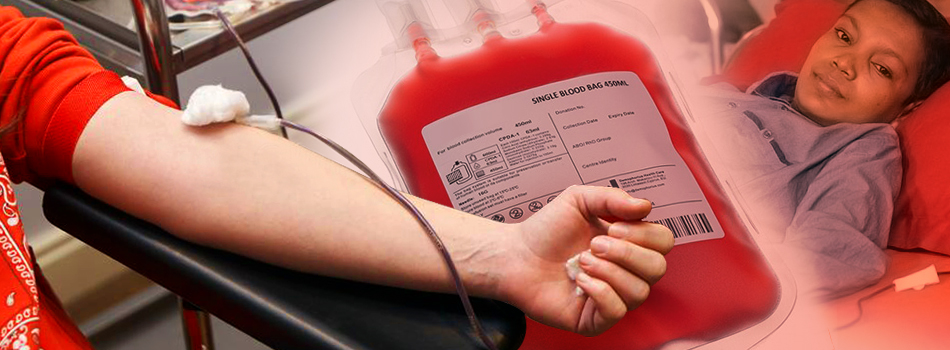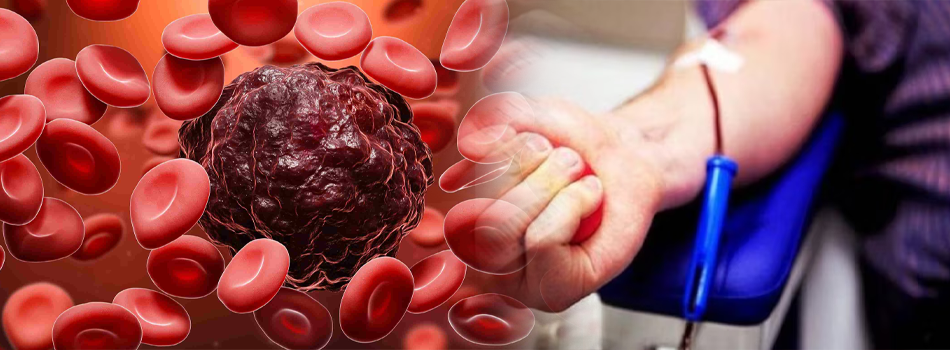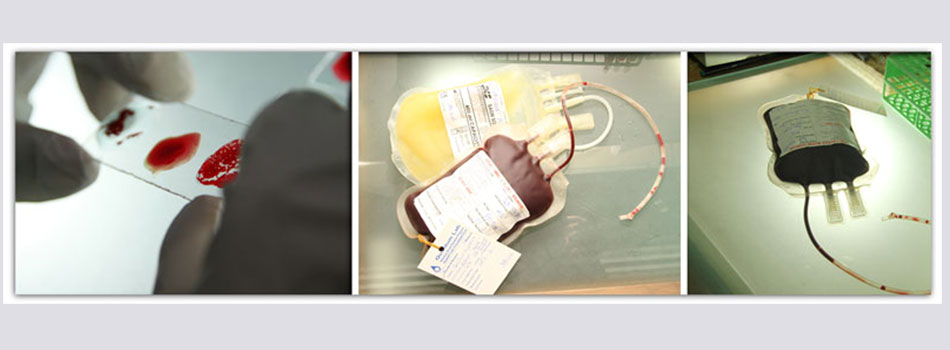মানবতার শ্রেষ্ঠ উপহার : স্বেচ্ছা রক্তদান
published : ২ নভেম্বর ২০২৫
আজ ২ নভেম্বর, ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস’। ১৯৯৬ সাল থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হচ্ছে দিবসটি।
স্বেচ্ছায় রক্তদান মানবকল্যাণের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত এবং যে-কোনো দেশের নিরাপদ রক্ত সরবরাহ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এটি এমন একটি উপহার, যা গ্রহীতার জীবন রক্ষা করে, কিন্তু দাতার কোনো ক্ষতি না করে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় রক্তের চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে, আর সেই চাহিদা মেটানোর প্রধান দায়িত্বটি বর্তায় স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের কাঁধেই।
রক্ত সঞ্চালনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
প্রথমবারের মতো সফল রক্ত পরিসঞ্চালনের পরীক্ষা চালান তরুণ চিকিৎসক ডা. রিচার্ড লোয়ার। তবে মানুষের নয়, কুকুরের। ১৬৬৫ সালে একটি কুকুরের ধমনী থেকে আরেকটি কুকুরের শিরায় সফলভাবে তিনি রক্ত পরিসঞ্চালন করেন।
১৬৬৭ সালে ফরাসী চিকিৎসক জ্যঁ ব্যাপ্টিস্ট ডেনিস ভেড়ার দেহ থেকে নয় আউন্স পরিমাণ রক্ত নিয়ে প্রবেশ করান দীর্ঘদিন ধরে জ্বরে ভুগছে এমন এক কিশোরের দেহে। একই পরীক্ষা আরো কয়েকজনের ওপর চালিয়ে সফল হলেও বাছুরের রক্ত ঢোকাতে গিয়ে মারা যান এ পরীক্ষার সর্বশেষ শিকার এন্টনি মৌরী।
সফলভাবে মানবদেহ থেকে মানবদেহে রক্ত সঞ্চালনের পথটি দেখিয়েছিলেন ব্রিটিশ ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ ডা. জেমস ব্লান্ডেল (Dr. James Blundell)। ১৮১৮ সালে, ডা. ব্লান্ডেল প্রথমবারের মতো সফলভাবে এক নারীর প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ (Post-partum hemorrhage) চিকিৎসার জন্য তার স্বামীর শরীর থেকে রক্ত নিয়ে তার দেহে সঞ্চালন করেন।
রক্ত সঞ্চালনের ইতিহাসে বাঁকবদল ঘটে ১৯০০ সালে যখন ট্রান্সফিউশন মেডিসিনের জনক নোবেলজয়ী জীববিজ্ঞানী ও চিকিৎসক কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার প্রথম রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার করেন। তার আগ পর্যন্ত অজানা ছিল কেন সবার রক্ত সবার শরীরে খাটে না। আবার একই গ্রুপের রক্ত নিলেও শারীরিক প্রতিক্রিয়া কেন হয়- এটা পরিষ্কার হয় ১৯৪০ সালের দিকে, যখন ডা. ল্যান্ডস্টেনারসহ কয়েকজন গবেষকের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হয় রক্তের রেসাস ব্লাড গ্রুপ সিস্টেম।
১৯১৬ সালে প্রথমবারের মতো সফলভাবে সংরক্ষিত রক্ত মানবদেহে প্রবেশ করানো হয়। এর ভিত্তিতে ফ্রান্সে বিশ্বের প্রথম ব্লাড ব্যাংকের সূচনা করেন আমেরিকান সেনা কর্মকর্তা ও মেডিকেল গবেষক অসওয়াল্ড হোপ রবার্টসন।
আর ১৯২১ সালে ব্রিটিশ রেড ক্রসের সেক্রেটারি পার্সি লেন অলিভারের (Percy Lane Oliver) উদ্যোগে লন্ডনের কিংস কলেজ হাসপাতালে তার সংগঠনের সদস্যরা সবাই একযোগে রক্ত দেন। এই উদ্যোগটিই ভিত্তি তৈরি করেছে আজকের দিনের স্বেচ্ছায়, বিনামূল্যে ও নিরাপদে রক্তদানের।
বাংলাদেশে স্বেচ্ছা রক্তদান
দেশে প্রথম রক্ত পরিসঞ্চালন হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৯৫০ সালে। ১৯৭২ সালের ১০ জুন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম নিজে রক্তদানের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সূচনা করেন। তৎকালীন বাংলাদেশ রেডক্রস (বর্তমানে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি) ১৯৭৩ সালে শুরু করে ব্লাড ব্যাংক কার্যক্রম।
১৯৭৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কিছু ছাত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘সন্ধানী’। শুরু হয় সাংগঠনিকভাবে বাংলাদেশে স্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোলন।
সরকারিভাবে ১৯৯৬ সালে গঠিত হয় ‘ব্লাড ট্রান্সফিউশন কমিটি’, যাদের কাজ ছিল রক্তদাতা নির্বাচনের মাপকাঠি নিরূপণ, নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন এবং রক্তের স্ক্রিনিং ও এ সম্পর্কিত প্রযুক্তি ব্যবহার কীভাবে করা যাবে তার প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেয়া।
১৯৯৬ সালে মোবাইল ডোনারদের সংগঠিত করার মাধ্যমে শুরু হয় কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। রোগীর প্রয়োজনে তখন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে গিয়ে রক্ত দিয়ে আসতেন কোয়ান্টামের তালিকাভুক্ত ডোনাররা।
ঢাকার কাকরাইলের ওয়াইএমসিএ ভবনে নিজস্ব ল্যাব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ২০০০ সালে। সিকি শতকের যাত্রায় কোয়ান্টাম গড়ে তুলেছে পাঁচ লক্ষাধিক স্বেচ্ছা রক্তদাতার সুসংগঠিত ডোনার পুল, যাদের অর্ধ-লক্ষাধিকই নিয়মিত রক্ত দেন। এখন পর্যন্ত কোয়ান্টাম সরবরাহ করেছে ১৭ লক্ষাধিক ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)। বাৎসরিক সরবরাহ লক্ষাধিক ইউনিট।
দেশে স্বেচ্ছা রক্তদানের বর্তমান চিত্র
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন কর্মসূচির তথ্য এবং বিভিন্ন বেসরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে মোট সংগৃহীত রক্তের মাত্র ৩০-৩৫% আসে স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের কাছ থেকে। বাকি ৬৫-৭০% আসে পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে, যারা নিজ রোগীর প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে থাকেন। এদের বলা হয় রিপ্লেসমেন্ট/রিলেটিভ ডোনার।
একটি পরিসংখ্যানমতে, দেশে স্বেচ্ছা রক্তদাতা সংখ্যায় মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ!
তবে এটা অনস্বীকার্য যে দেশে স্বেচ্ছা রক্তদানের হার বেড়েছে, ফলশ্রুতিতে কমেছে পেশাদার রক্তদাতাদের দৌরাত্ম্য। ২০০০ সালে আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় রক্তের ৪৭ ভাগই আসত পেশাদার রক্তদাতাদের কাছ থেকে। ২০১৭ সালে তা এসে দাঁড়ায় শতকরা মাত্র ১২ ভাগে!
স্বেচ্ছা রক্তদান কেন প্রয়োজন?
নিরাপদ রক্ত সরবরাহের মূল ভিত্তি হলো স্বেচ্ছায় ও বিনামূল্যে দান করা রক্ত। কারণ তাদের রক্ত তুলনামূলকভাবে নিরাপদ এবং এসব রক্তের মধ্য দিয়ে গ্রহীতার মধ্যে জীবনসংশয়ী সংক্রমণ যেমন- এইডস, হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি সহ অন্যান্য রক্তরোগ সংক্রমনের আশংকা খুবই কম।
একটি দেশের স্বাস্থ্যসেবার মান নির্ভর করে তার নিরাপদ রক্তের মজুতের ওপর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) নির্দেশিকা অনুসারে, একটি দেশের মোট জনসংখ্যার ১ থেকে ৩ শতাংশ যদি নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদান করে, তবে সেই দেশের রক্তের চাহিদা মিটে যায়।
বাংলাদেশে প্রতি বছর বিভিন্ন সার্জারি, সড়ক দুর্ঘটনা, জটিল প্রসবকালীন পরিস্থিতি এবং থ্যালাসেমিয়াসহ অন্যান্য রক্তজনিত রোগের চিকিৎসার জন্যে প্রায় ৮-১০ লক্ষ ইউনিট (ব্যাগ) রক্তের প্রয়োজন হয়। বেঁচে থাকার জন্যে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের নিয়মিত রক্ত লাগে।
আমাদের দেশে তরুণদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। তাদের মধ্যে ২ শতাংশ যদি বছরে মাত্র একবারও রক্ত দেন, তাহলেই মিটবে রক্তের চাহিদা, রক্তের অভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে না কোনো মুমূর্ষু রোগীকে।
স্বেচ্ছায় রক্তদান দাতার জন্যেও উপকারি। নিয়মিত রক্তদান শরীরের অতিরিক্ত আয়রনের মাত্রা কমিয়ে হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। আর রক্তদানের আগে দাতার রক্তে হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, এইডস (HIV)-সহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ আছে কি না তা স্ক্রিনিং হয়ে যায়।
রক্তদান বিশাল পূণ্যের কাজ
তাই আপনি যদি ১৮-৬৫ বছর বয়সী হয়ে থাকেন, ওজন যদি নূন্যতম ৪৫ কেজি হয়ে থাকে এবং রক্তস্বল্পতা বা অন্য কোনো রোগ না থাকে তাহলে রক্তদান শুরু করুন। একজন সুস্থ মানুষ প্রতি চার মাস অন্তর রক্তদান করতে পারেন। রক্তদানের ঘাটতি পূরণ হয়ে যায় এই সময়টুকুতে।
রক্তদান কোনো দুঃসাহসিক কাজ নয়, এটি একটি সহজ ও নিরাপদ অভ্যাস। সামান্য একটু সুঁইয়ের খোঁচা, ১০ মিনিট সময় এবং এক ব্যাগ রক্ত পারে পৃথিবীতে একটি অমূল্য প্রাণকে একটি নতুন সকাল উপহার দিতে। আপনি চলে গেলেও আপনার দেওয়া রক্ত অন্য একজনের দেহে হয়ে উঠবে জীবনের প্রতীক।
আরো পড়ুন